ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস:১৮৫৭-১৯৪৭
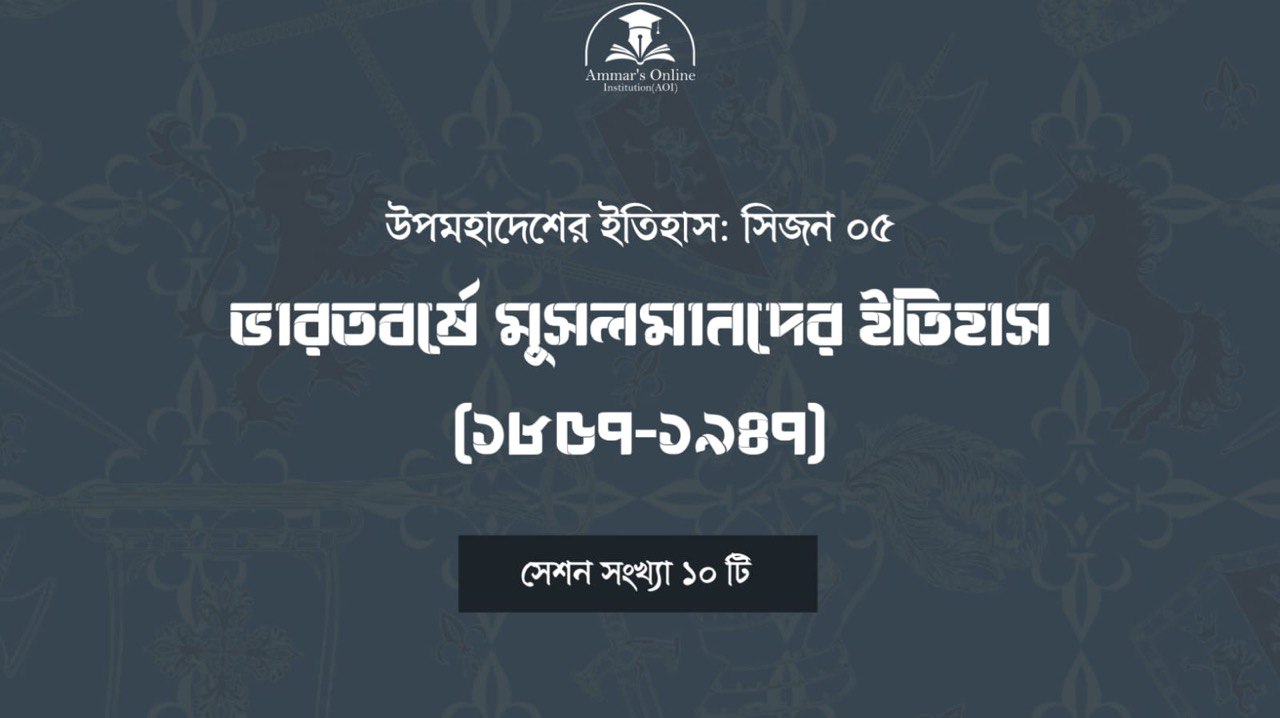
কোর্সের বিস্তারিত :
ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল ছিল ঘটনাবহুল। লালকেল্লার ভেতরে মুঘল সূর্য শেষবারের তার আভা ছড়াচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা দখল করছিল একের পর এক এলাকা, মহীশুরের বাঘ টিপু সুলতানের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে নিভে যায় প্রতিরোধের শেষ অগ্নিশিখাও। মধ্যভারত জুড়ে মারাঠা আধিপত্য, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে শিখদের ত্রাস, দিল্লিতে উদাসিন মুঘল সম্রাট, এর মাঝে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটে বাহিনী ধীর কদমে এগিয়ে আসছিল দিল্লির দিকে। প্রতাপশালী মুঘলদের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লি শীঘ্রই ইংরেজদের করতলগত হয়, সম্রাট পরিণত হন কাগুজে বাঘে। বার্ষিক পেনশনভোগী মুঘলরা এক আশ্চর্য জগত গড়ে নিলেন লালকেল্লা ও দিল্লিকে ঘিরেই। সেদিনের দিল্লি যেন হঠাত জেগে উঠলো বিপুল বৈভবে।
শাহ ওয়ালিউল্লাহর ইন্তেকালের কয়েক দশক পার হলেও দিল্লির ইলমি নেতৃত্ব ছিল তার খান্দানের হাতেই। শাহ আবদুল আজিজের দরসগাহ হয়ে উঠেছিল ইলমে নববীর প্রাণকেন্দ্র। সেই টানে এসে জুটলেন সাইয়েদ আহমদ শহিদ। জিহাদি আন্দোলনের ধারার সূচনা ঘটে গেল সেখানেই। পরবর্তী তিন দশক ধরে জিহাদি আন্দোলনের মূল মারকাজ থাকলো দিল্লিতেই, শাহ মুহাম্মদ ইসহাক আরবে হিজরত করার আগ পর্যন্ত। জিহাদি কাফেলার দাঈরা ছুটলেন ভারতের সর্বত্র, হিন্দুয়ানি রুসম রেওয়াজের সামনে সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাড়ালেন তারা। বাংলায় শুরু হলো ফরায়েজি আন্দোলন, তাদের সাথে তর্কে জড়ালেন সাইয়েদেরই খলিফা কারামত আলি জৌনপুরি। সেকালের রাজনীতিতে সাইয়েদের উলটো পথে হেটেছিলেন অনেক খলিফাই। জিহাদ বিরোধি ফতোয়া দিলেন জৌনপুরি, কৌশলী ইংরেজ ফতোয়া নিল নজদি বিরোধী আলেম আহমাদ যাইনি দাহলানেরও। সাইয়েদের পথ থেকে নিরাপদ দুরত্বে থেকেছিলেন নবাব সিদ্দিক হাসানের বাবা আওলাদ হাসান কন্নৌজিও। জিহাদি আন্দোলনের প্রভাব শুধু রাজনৈতিকই ছিল না, এর প্রভাব পড়েছিল সাহিত্যেও। উর্দু আদব মে ওহাবি লিটারেচারের পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নয়। মুমিন খাঁ মুমিন, হায়দার আলি রামপুরি, ফৈয়াজ আহমদ সাদেকপুরি কিংবা আবদুল্লাহ খাঁ তালাবিদের হাত ধরে উর্দু গদ্যের যাত্রা শুরু হয় ১৮৫৭ সালের অনেক আগেই। প্রফেসর আইয়ুব কাদরি, কালিমুদ্দিন আহমদ কিংবা খাজা আহমদ ফারুকি সবাইই একমত, এই লেখকদের রচনা ওহাবি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা।
সেদিনের দিল্লিতে ছিলেন ভারতের প্রভাবশালী মেধাবী ব্যক্তিবর্গ। মির্জা মাজহার জানে জানার খানকায় ছিলেন তার সাজ্জাদানাশিন শাহ গোলাম আলি। সেই যে নবাব আমির খাঁর দানের অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে সাফ জানিয়েছিলেন, মা আবরুয়ে ফকর কানাআত নমি বুরেম, বামীর খাঁ বগোয়ে কে রুজি মুকাররারাস্ত। দিল্লি কলেজে পড়াচ্ছিলেন মাওলানা মামলুক আলি, তার কাছে ছুটছেন কাসেম নানুতুবি, ডেপুটি নজির আহমদের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। শাহ মুহাম্মদ ইসহাক চলে গেছেন, তার মসনদে বসেছেন মিয়া নজির হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভি। তার কাছে হাদিস পড়তে আরব থেকে ছুটে এসেছেন সাদ বিন হামদ বিন আতিক, ইসহাক বিন আব্দুর রহমান ইবনে হাসান বিন মুহাম্মদ। পরের জন তো সম্পর্কে ইবনে আবদুল ওয়াহাবের প্রপৌত্র।
খানদানে ওয়ালিউল্লাহর দরসগাহ থেকে বের হলেই হয়তো চোখে পড়বে কবি ইবরাহিম যওককে, গালিবের সাথে মুশায়রা করতে ছুটে যাচ্ছেন লালকেল্লা, অথবা মুফতি সদরুদ্দিন আযুর্দার ঘরে। আছেন মুস্তফা খান শেফতা, হালি, এলাহাবাদি, দাগ দেহলভি, রাফি সওদাও। সেদিনের দিল্লিতে উর্দু কাব্য আরো প্রসারিত হচ্ছে, ডালপালা মেলছে। রেখতা থেকে উর্দুর দিকে এ যেন ধীর পদক্ষেপ। গদ্যেও পিছিয়ে নেই, তাহযিবুল আখলাকে একের পর এক লেখা হচ্ছে সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। ৭০ বছর পর আলীগড়ে এসে আবুল কালাম আজাদ স্বীকার করবেন উর্দুর কাঠামোতে আধুনিকতার প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিল তাহযিবুল আখলাকের লেখকরাই।
শুধুই কি দিল্লি, সমগ্র ভারত জুড়েই যেন চলছে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ, একের পর এক সংস্কার আন্দোলন। দীর্ঘ ঘুমের পর যেন চোখ মেলে তাকাচ্ছে ভারতবাসী। রাজা রামমোহন রায়, ব্রাক্ষ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ সবাই সক্রিয় সমানতালে। দুহাতে লিখছেন স্যার সৈয়দ, তাকে পাল্লা দিচ্ছেন সৈয়দ আমির আলি। আছেন স্প্রিঙ্গার ও টমাস আর্নল্ডও। নতুন করে বিকশিত হচ্ছে প্রকাশনা শিল্প। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি, নওল কিশোর প্রেস লখনৌ, দাইরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়া, ছাপছে একের পর এক তুরাস।
এই শতাব্দিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল মাদরাসা ফয়জে আম কানপুর, মাদরাসা আহমদিয়া আরা, দারুল উলুম দেওবন্দ, নদওয়াতুল উলামা লখনৌ। ধ্রুবতারার মত আবির্ভুত হলেন শিবলি নুমানি, মির্জা হায়রত দেহলভি, নবাব হাবিবুর রহমান খান শেরওয়ানি। স্বল্প হায়াতে অসাধারণ বরকত নিয়ে এলেন আবদুল হাই লখনবী। উলামায়ে ফিরিঙ্গি মহলের শানদার কারনামায় যুক্ত হলো নতুন ফলক। ভূপালের বিধবা নবাবকে বিয়ে করে নবাব হলেন সিদ্দিক হাসান খান কন্নৌজি। লখনৌবির সাথে বারবার বিতর্কে জড়ালেন তিনি, ইলমি দুনিয়ায় দিলচসপ বাত হিসেবে টিকে রইলো সেসব আলাপ। নবাব সিদ্দিক হাঁসানের চেষ্টায় ভূপাল হয়ে উঠলো হাদিসের অন্যতম দরসগাহ, ছুটে এলেন শাওকানির ছাত্ররাও।
শাহ ইসমাইল শহিদের লেখা নিয়ে বিতর্কের রেশ ধরে আত্মপ্রকাশ করলো বেরেলভি ধারা, রায়বেরেলির ঈদের জামাতের দ্বন্দ্ব যেন প্রকাশ্যে আসার সুযোগ করে দিল মারকুটে সব ইলমি তর্ক। আলি নকি খানের পর হাল ধরলেন আহমদ রেজা বেরেলভি। একের পর এক তাকফিরে হৈ চৈ ফেলে দিলেন সর্বত্র। আহলে হাদিস, দেওবন্দি, বেরেলভি দ্বন্দ্বের মাঝেই আগমন ঘটলো কাদিয়ানীর, রুখে দাঁড়ালেন আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভি। হাদিস অস্বীকার করে বসলো চেরাগ আলি, ধাওয়া চললো তার দিকেও। উর্দু সাংবাদিকতায়ও তখন উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত। পিতার ফাসির পর পলাতক মুহাম্মদ হুসাইন আজাদও মেলে ধরেছেন নিজেকে।
শতাব্দির মাঝামাঝি ঘটে গেল ঐতিহাসিক গদর। রক্ত ও খুনের মাঝে ইংরেজ দমন করলো সে সংগ্রাম। লালকেল্লা ছেড়ে রেংগুনে নির্বাসিত হলেন বাহাদুর শাহ জাফর। অস্ত গেল মুঘল সূর্য। ভাগ্যবিড়ম্বিত গালিব সেই ক্ষোভ ঝাড়লেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর।
এরপর? এরপর কী হলো? ১৮৫৭ থেকে কীভাবে ১৯৪৭ এলো? রক্ত মাটির এই দ্বৈত লড়াইয়ের আদি ও আসল রূপ জানতে হলে আমাদের প্রয়োজন ইতিহাসের সবদিকে আলো ফেলা, সবকিছু নির্মোহভাবে দেখা। আর এই চিত্র ইতিহাস আলোচক ইমরান রাইহান এর চেয়ে ভালো আর ফুটিয়ে তুলতে পারে!
তাই আমাদের ইতিহাস ০১ সিরিজের উপমহাদেশের ইতিহাস সিজন ০৫ এর এবারকার আয়োজন – ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)।
কোর্স ইন্সট্রাক্টর: ইমরান রাইহান
লেখক-অনুবাদক ও ইতিহাস আলোচক
কোর্স মডিউল:
১। ১৮৫৭ পরবর্তী ভারতীয় মুসলমান সমাজ
২। দেওবন্দ আন্দোলন
৩। আলিগড়ি ধারা
৪। নদওয়াতুল উলামা
৫। আর্য সমাজ ও মুসলমানদের মাঝে প্রভাব
৬। উর্দু সাহিত্যে নতুন যুগ
৭। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতীয় মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা
৮। বাংলার মুসলিম সমাজ
৯। সমকালীন রাজনীতি (মুসলিম লিগ, খাকসার তেহরিক, খোদাই খেদমতগার, মজলিসে আহরার, জামায়াতে ইসলামি, কংগ্রেস)
১০। দেশভাগ
কোর্সটি থেকে কী শিখবেন?
- ১৮৫৭ পরবর্তী সময় থেকে দেশভাগের আগপর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস।
কোর্স কন্টেন্ট
উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)
-
১৮৫৭ পরবর্তী ভারতীয় মুসলমান সমাজ
52:55 -
দেওবন্দ আন্দোলন
52:53 -
আলীগড়ি ধারা
25:20 -
নদওয়াতুল উলামা
36:57 -
আর্যসমাজ ও মুসলমানদের মাঝে প্রভাব
33:18 -
উর্দু সাহিত্যে নতুন যুগ
30:11 -
বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতীয় মুসলমানদের জ্ঞান চর্চা
22:58 -
বাংলার মুসলিম সমাজ
38:12 -
সমকালীন রাজনীতি
34:22 -
দেশভাগ
42:52 -
লেকচার নোট
00:00
ভর্তির জন্য মেসেজ করুন আমাদের ফেসবুক পেইজে। পেইজে যাওয়ার জন্য নিচের বাটনে ক্লিক করুন
-
LevelIntermediate
-
Total Enrolled7
-
Duration6 hours 12 minutes
-
Last UpdatedJuly 29, 2025


